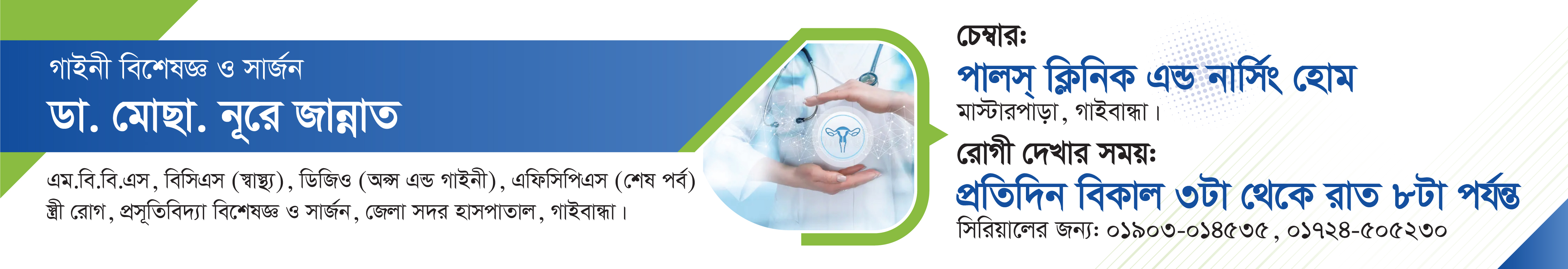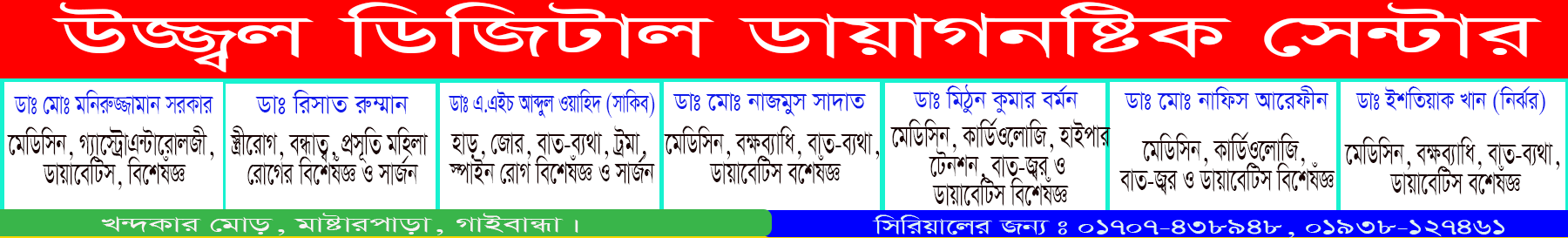ছাত্র রাজনীতির সত্যসংক্রান্তি
ছাত্র রাজনীতি

শেখ মাসুকুর রহমান শিহাব: ছাত্র রাজনীতি, এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত অথবা সমালোচিত বিষয়গুলোর একটি। ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে কি হবে না বা মূল রাজনৈতিক দলের বলয়ে থাকবে কিনা এসব বিতর্ক অনেক পুরাতন কিন্তু সবসময়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। এই আলোচনাগুলো সবচেয়ে বেশি সামনে আসে যখন দেশের কোন প্রান্তে বা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের দারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত অছাত্র সুলভ আচরণ কিংবা প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাসী সুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়।
বুয়েটে আবরার ফাহাদ হত্যা কান্ডের পর ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আলোচনা বেশ প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষার্থীদের মাঝে। পিটিয়ে মারা, হত্যার পরে মৃত ফাহাদকে নিয়ে টালবাহানা মানুষের মনে এতটাই দাগ কাটে যে, একটা ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক চর্চা বন্ধ করার কতধরনের প্রভাব প্রথমে সেই ক্যাম্পাস ও পরে সমগ্র জাতির উপর পরতে পারে সেটা ভাবার সময়ই আমাদের হয় নি।
পৃথিবীর সব দেশেই রাজনৈতিক বলয় টিকে রখতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উপর ভর করে থাকে রাজনৈতিক দলগুলো। এমনকি বৃটিশ রাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে যখন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা ছোট ছোট দলে সংগঠিত হচ্ছিল, তখন কৃষক বিদ্রোহ প্রধান শক্তি হিসেবে দেখা দিলেও শেষ দিকের চূড়ান্ত লড়াইয়ে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ প্রধান শক্তিতে রুপান্তর হতে থাকে। তা সে সশস্ত্র বা অহিংস, যে আন্দোলনই হোক না কেন।
প্রথম ভারত বিভাজনের পরে অর্থাৎ পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই যখন স্বাধীন বাংলা অপরিহার্য হয়ে পরে, তার প্রতিটি আন্দোলনেই ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল খুব জরুরি। সমাজের সব স্তরের মানুষ ছাত্র শক্তির উপর এতটা আস্থা অর্জন করেছিল যে, তারাই আন্দোলনের বিস্তার ঘটানো দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে পরে।
স্বাধীনতার সংগ্রামের পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এর ভিন্ন রুপ আসে নি বরং ছাত্র রাজনীতি আরো প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে দাঁড়ায় গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে। এমকি যাদের এখন বিভিন্ন দলের প্রধান নেতা হিসেবে দেখা যায়, যারা রাজনীতি বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, সকলেই ছাত্র রাজনীতির অধ্যায় পেড়িয়ে আশা। ৯০'র আন্দোলনে বিস্ফোরক হয়ে পরে ছিল ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ঘোষণা। এমনকি সেই সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক রুপ নেবার ছল করার সময় বাধ্য হয়েছিল তার দলে ছাত্র সংগঠন শুরু করার।
বলা হয়ে থাকে, নব্বই পরবর্তী গণতন্ত্রের মোড়কের প্রতিটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল চেষ্টা চালিয়ে গেছে ছাত্র রাজনীতির এই ভর কেন্দ্রকে ব্যবহার করে টিকে থাকতে কিন্তু ধিরে ধিরে তাদের এই ভর করা ঠেলে দিয়েছে অন্ধকারের দিকে। একটা সময় যে অভিভাবকরা গর্বের সাথে উচ্চারণ করতো সন্তান রাজনীতি করে, এখন সেখানে অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদের আড়াল করে রাজনীতি থেকে। যেখানে ছাত্র রাজনীতি ছিল আমাদের প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার, সেখানে এখন “i hate politics” প্রজন্ম বাড়ছে। আর কেনই বা বাড়বে না! ক্যাম্পাসগুলো যখন অনিরাপদ হতে হতে সন্ত্রাসের আতুরে পরিণত হতে থাকে। সংঘর্ষ এড়াতে ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিতে হয় এবং সেই এজেন্ডাও বাস্তবায়ন করতে ছাত্র নামের এক শ্রেনীর মহড়া দেয়, তখন সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ভাবে পিছিয়ে পরবে লড়াই থেকে।
এত গেল, ছাত্র রাজনীতির হালচাল কিন্তু কেন একটা ক্যাম্পাসে সাধারণ কোন সংগঠন গড়ে তোলার সাথে সাথেই রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন থাকা জরুরি? কেন বুয়েট ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে না এমনকি বাংলাদেশের যেকোনো ক্যাম্পাসে যদি রাজনীতি বন্ধ করা হয়ে থাকে কৌশলে, তাহলে তা আবার শুরু করা দরকার?
বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে শুধু ফাহাদের মৃত্যু হয়নি, একই সাথে মৃত্যু হয়েছে হত্যার সাথে জড়িত ২৫ শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ ও ভবিষ্যৎ, মৃত্যু হয়েছে ২৬টি পরিবারের স্বপ্নের, ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে দাঁড় করিয়েছে ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র রাজনীতির পরিবেশের। একই ভাবে ছাত্র নেতাদের এমন অপরাজনীতির বলি হয় হাজার স্বপ্ন। আর ক্যাম্পাসগুলোতে এমন রাজনৈতিক দোলাচলের সুযোগে ক্যাম্পাসে ভর করে মৌলবাদী সংগঠনসহ স্বাধীনতার চেতনা বিরোধীদের ঝাঁক। যারা স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশে কার্যক্রম চালাবার সুযোগ পায় না।
মেনে নেয়া কঠিন হলেও আমরা জানি, অনিয়ম আর দূর্ণীতি আমাদের সমাজের রন্ধে রন্ধে ঢুকে আছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও মুক্ত না। বাস্তবতা হচ্ছে শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই জড়িত থাকে এসব অনিয়ম দূর্নীতিতে, তাহলে প্রতিবাদ আসবে কোথা থেকে? এখানেই আবশ্যক হয়ে পড়ে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের, সাধারণ সাংস্কৃতিক সংগঠন আর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো নানান সীমাবদ্ধতায় ধারাবাহিক প্রতিবাদ ও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম না বর্তমান পরিস্থিতিতে। তবে নিশ্চিত ভাবেই রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন নিয়েই প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়।
আবার রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যার মধ্যে আমাদের শিক্ষা শিক্ষা ব্যাবস্থাও। আমাদের শিক্ষা নীতি কি হবে, শিক্ষার কারিক্যুলাম কি হবে, শিক্ষা কতটা সহজলভ্য হবে, সমাজের কোন শ্রেনী কতটা শিক্ষা পাবে, শিক্ষার ব্যয় এমকি শিক্ষকদের বেতন কাঠামোও রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত যদি শিক্ষার পরিবেশ বা জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় অথবা তার বিপরীতে হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা বা আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ করবে কে? একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মোকাবেলা আপনি যে নামেই অবহিত করুন না কেন, সেটা মূলত একটা রাজনৈতিক কার্যক্রম। এমনকি বুয়েটে যে রাজনৈতিক সংগঠন বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে, সেটিও একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। বরং প্রশ্ন তোলা যেতো রাজনীতির নামে অপরাজনীতি আর সহিংসতা রোধে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়। সেটা ক্যাম্পাস ও রাজনৈতিক দলগুলো একক বা যৌথ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হতে পারে। মাথা ব্যাথার সমাধান মাথা কেটে ফেলে দেয়ার মতো সিদ্ধান্ত অজ্ঞতা ছাড়া কিছু না।
ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র রাজনীতির অগ্নি পরিক্ষা ছিল ছাত্র সংসদ। জাতীয় ইস্যু বা অধিকারের প্রশ্নে নিজেদের অঙ্গিকার সামনে রেখে রাজনৈতিক চর্চা এবং সংগঠনকে জনপ্রিয়করণ এবং সংসদে ক্ষমতায়ন করতে হতো, যার ফলে অযাচিত বক্তব্য ও আচরণ থেকে বিরত থাকা এবং আভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিকতায় সাংগঠনিক চর্চা যে উচ্চতায় ছাত্র নেতাদের নিয়ে যেত তাতে একেকজন ছাত্র নেতা উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতো। ছাত্র সংসদ বিকশিত করতো একজন ছাত্রনেতার সহনশীল আচরণ, সৌহার্দ্যের মানসিকতা, নেতৃত্বের কৌশলসহ নানান গুণাবলি। ছাত্র সংসসদের অনুপস্থিতিতে সংগঠনগুলোতে মূল রাজনৈতিক দলের একছত্র প্রভাব ফেলেছে, ছাত্র নেতাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা খর্ব করেছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের কাছে দায়বদ্ধতা না থাকায় বাড়ে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব।
ছাত্র সংসদ বন্ধ হওয়া, ক্ষমতা কেন্দ্রিক দলগুলোর স্বদিচ্ছের অভাব, ক্ষমতায় টিকে থাকতে ছাত্র সংগঠনগুলোকে যথেচ্ছা ব্যবহার ও অনৈতিক সুবিধা দেয়া রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোকে করে তুলেছে সহিংস আর সুবিধাভোগী। যার ফলে ছাত্রনেতাদের মানুষ মনে করে এখন চাঁদাবাজ আর সন্ত্রাসী। গৌরব দিনগুলোর ইতিহাস আর গল্প বক্তৃতায় থাকলেও কর্মকাণ্ডে তা দেখা যায় না। ফলে অভিভাবক, এমনকি সাবেক ছাত্র নেতারাও চায় না তাদের সন্তানরা যুক্ত এই রাজনীতিতে। বিশ্লেষণ বলছে, ছাত্র সংসদ আর ছাত্র রাজনীতি কৌশলে নষ্ট করেছে নব্বই পরবর্তী ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলো। অথচ এই ছাত্র রাজনীতিই তৈরি করেছে বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে জাতীয় চার নেতাসহ সিরাজুল ইসলাম খান, সৈয়দ আশরাফ, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মতিয়া চৌধুরীসহ জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের। রাষ্ট্রের মাঝি, কাণ্ডারী তৈরি করে যে ছাত্র রাজনীতি, হটকারিতায় সেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে নেতৃত্ব শূন্য একটা জাতি প্রবেশ করবে অপার অন্ধকারে আর আমলাতান্ত্রিক ভরশুন্য সময়ে।
ছাত্র রাজনীতির পুরো ক্ষেত্রেই আতঙ্কের নাম হতে পারে না। গৌরবের দিনগুলোর মতো আগামীর সংগ্রামের কি ছাত্র রাজনীতি ভূমিকা রাখবে না? অথবা মেহনতি মানুষের গান গলায় নিয়ে ফেরিওয়ালা হয়ে গ্রামের হাটবাজার বা শহরের অলিগলি কি ছাত্রনেতাদের উদ্দীপনায় ভাসবে না?
আজও দেশের আনাচে-কানাচে শিক্ষার অধিকারসহ জনগণের নাভিশ্বাস জীবনের মুক্তির শ্লোগান ছাত্ররা দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে। ভবিষ্যতের সমাজ নির্মাণের তাদের শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যেমন জরুরি, তেমন জরুরি অভিভাবকদের অংশগ্রহণ যেন “i hate politics” প্রজন্ম দাঁড়িয়ে না যায় বরং রাজনীতিকে ভালোবেসে সুদ্ধ চর্চায় চলতে পারে। শিক্ষার্থীদেরকেই খুঁজে নিতে হবে কারা সত্যিকারের রাজনীতি করতে চায়, কারা শিক্ষার্থীদের অধিকারে লড়াই করে, কারা ‘ঘরে খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে যাচ্ছে’ এবং তারা কি বার্তা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারা রাজনীতির নামে অপরাধী তৈরি করে এবং কিভাবে তাদের বিলীন করা যায়। অন্যথায় রাজনীতি বিমুখীকরণের শেষ পরিনতি আঘাত করবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যতে। পরিবর্তনের চাহিদায় এর বিকল্প অসম্ভব।
লেখক: সাবেক ছাত্র নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মী, মুঠোফোন: ০১৭৫৬ ০৯৬৯৫২, মেইল: mashuq1992@gmail.com